জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১
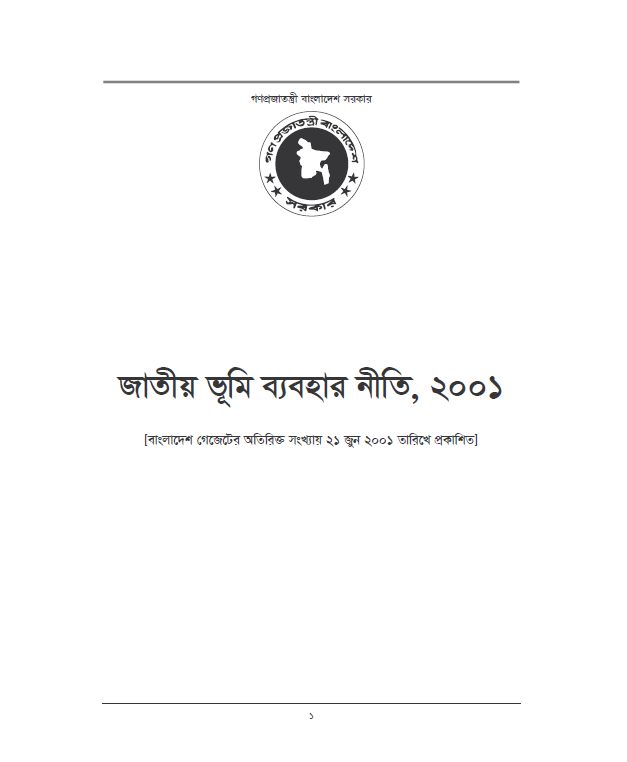
বিস্তারিত / তফসিল
[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২১ জুন ২০০১ তারিখে প্রকাশিত]
বিজ্ঞপ্তি
তারিখ, ১৩ জুন ২০০১ ইং
নং-ভূঃ/শা-৫/ভূমি নীতি/০১/২০০০/১৫০।-জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা বিষয়ে সরকার নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা প্রনয়ন করিয়াছে। এতদ্বারা অনুমোদিত নীতিমালা সকলের অবগতির জন্য জারী করা হইল। গেজেট প্রকাশনার তারিখ হইতে নীতিমালা কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এম সাইফুল ইসলাম
সচিব
জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, বাংলাদেশ
১. প্রেক্ষাপট:
১.১ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এদেশের এক-তৃতীয়াংশ জাতীয় আয়ের উৎস এবং দুই-
তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। তাই বাংলাদেশে ভূমি ও পানিসম্পদের গুরুত্বও অপরিসীম। ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির সব কিছুরই উৎস। ১৪.৪ মিলিয়ন হেক্টরের বাংলাদেশে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন মানুষের বাস, প্রতিজনে ভূমির পরিমাণ গড়ে ২৭ শতক এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৭ শতক মাত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়ণের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পোন্নয়ন ঘটছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ক্রমাগত সম্প্রসারণ হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ২০.২ মিলিয়ন একর যা ১৯৯৭ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১৭.৫ মিলিয়ন একরে। ভূমির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার এবং চাষযোগ্য জমির অন্যবিধ ব্যবহারের একটি চিত্র নিচের ছক দুটি থেকে পাওয়া যাবে:
ছক-১
বাংলাদেশ: ভূমি প্রাপ্যতা ও ব্যবহার, ১৯৭৪-১৯৯৬
| (হাজার একরে) | (মোট জমির শতকরা অংশ) | |||||
| বৎসর | ১৯৭৪ | ১৯৯০ | ১৯৯৬ | ১৯৭৪ | ১৯৯০ | ১৯৯৬ |
| মোট জমির পরিমাণ | ৩৫,২৮২ | ৩৭,৫২১ | ৩৬,৬৬৪ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
| চাষযোগ্য জমি (নীট আবাদী+কৃষিযোগ্য পতিত) | ২৩,১৯৯ | ২৩,২০৯ | ২১,৫৬০ | ৬৬ | ৬২ | ৫৯ |
| নীট আবাদী | ২০,৯৭৭ | ২১,৮৩৭ | ১৯,২৮০ | ৫৯ | ৫৮ | ৫৩ |
| কৃষিযোগ্য পতিত | ২,২২১ | ১,৩৭২ | ২,২৮১ | ৭ | ৪ | ৬ |
| বনাঞ্চল | ৫,৫০৮ | ৪,৫৯১ | ৫,৩১৫ | ১৬ | ১২ | ১৪ |
| কৃষি অযোগ্য | ৬,৫৭৬ | ৯,৭২১ | ৯,৭৮৮ | ১৯ | ২৬ | ২৭ |
তথ্যসূত্র: বিবিএস বাংলাদেশ, ১৯৯৮
ছক-২
(হাজার একরে)
| বৎসর | ১৯৮৩-৮৪ | ১৯৯৭ |
| চাষযোগ্য জমি | ২২,৬৭৪ | ২০.২০৯ |
| আবাদি জমি | ২০,২৩৮ | ১৭,৪৪৯ |
| কৃষিযোগ্য পতিত | ২,৪৩৬ | ২,৭৬০ |
| বাড়ীঘর | ৮৫৭ | ১,০২৭ |
তথ্যসূত্র: বিবিএস বাংলাদেশ, ১৯৯৮।
১.২ ভূমি ও পানিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। ভূমি, পানিসম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশজ উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে এ তিন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সমন্বয় সাধন তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব।
১.৩ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জন এবং দেশজ সম্পদের সার্বিক ও রপ্তানীমুখী উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭ ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দেশের দুটি প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ যথা-ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। নিবিড় কৃষি কার্যক্রম, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানসহ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।
২. ভূমি ব্যবহার নীতির উদ্দেশ্যাবলী:
ক. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কৃষি জমির সার্বিক পরিমাণ বিভিন্ন কারণে উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার বর্তমান ধারা প্রতিহত করা;
খ. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমির প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে "জোনিং” ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে অপরিকল্পিতভাবে আবাসিক এলাকা সম্প্রসারণ, শিল্প স্থাপন ও বিপণন কর্মকাণ্ডের বর্তমান প্রক্রিয়া যুক্তিসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ;
গ. ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নদী, হাওর বা সমুদ্রবক্ষে জেগে ওঠা চরভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
ঘ. বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে এরূপ জমি বিশেষ করে সরকারি খাস জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;
ঙ. ভূমির ব্যবহার যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা;
চ. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
ছ. প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণ করা, নদী ভাঙন রোধ করা, পাহাড় টিলাভূমি কর্তন প্রতিহত করা;
জ. ভূমিদূষণ প্রতিরোধ করা;
ঝ. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য বহুতলবিশিষ্ট দালান নির্মাণের মাধ্যমে স্বল্প পরিমাণ জমির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৩. ভূমি ব্যবহারভিত্তিক জোন নির্ধারণ:
৩.১ ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং যথেচ্ছ ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহার্য জমির এলাকা ভিত্তিক চিহ্নিত করা। দেশের সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহ নাগরিক সুবিধা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল সকল নাগরিকের জন্য সহজপ্রাপ্য করার জন্য কাজ করে থাকে। আবাসিক এলাকার অবস্থান বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকা থেকে একটু যুক্তি সংগত দূরত্বে থাকা বাঞ্ছনীয়। নিরাপদ ও দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থার ওপরও এই দূরত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল।
৩.২ Town Improvment Act, 1953 এর বিধান সত্ত্বেও বড় শহরগুলোতে বহু ক্ষেত্রেই আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠেনি। আবাসিক এলাকা হিসাবে চিহ্নিত জায়গায় অসংখ্য দোকানপাট, মার্কেট, ক্লিনিক ছাড়াও ছোট ছোট শিল্পকারখানা স্থাপিত হচ্ছে। এই অনভিপ্রেত অবস্থার আশু অবসান কাম্য।
৩.৩ শহরাঞ্চলে যদিও কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃশ্যমান, গ্রামাঞ্চলে তা একেবারেই অনুপস্থিত। মূল্যবান কৃষিজমি ভরাট করে গ্রাম সম্প্রসারিত হচ্ছে, ছোট বাজার স্ফীত হয়ে গ্রাস করছে সংলগ্ন ফসলী জমি, ছোট ও কুটিরশিল্প স্থাপনের জন্য সরকার অনুমোদিত শিল্পনগরী খালি রেখে কলকারখানা বসছে মালিকের বসতবাটির নিকটবর্তী স্থানে। এই অবস্থা নিরসনের লক্ষে Village Improvment Act নামে একটি নতুন আইন প্রবর্তন করা যেতে পারে। গ্রামীণ অবকাঠামো বিশেষ করে পরিকল্পিত আবাসনের জন্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৩.৪ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার অপরিহার্যতা বিবেচনা করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আবাসিক এলাকা নিরূপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর জন্য জায়গা পূর্বাহ্ণেই নির্দিষ্ট করা সম্ভব। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ইতিমধ্যেই যে সব জমি, বনভূমি, টিলা শ্রেণীর জমি, জলাভূমি বা বিশেষ ধরনের বাগান হিসাবে পরিচিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া সেগুলির প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন আনা যাবে না অর্থাৎ ভরাট করে আবাসিক এলাকা সৃষ্টি বা শিল্পায়ন ইত্যাদি করা যাবে না।
৩.৫ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য জমির একটা জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করবে। মূলত আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসাবে একেকটি জোন চিহ্নিত হবে। এর ফলে সামগ্রিক নগর জীবন একটা সুবিন্যস্ত আঙ্গিকে প্রসার লাভ করবে।
৩.৬ শহর এলাকার বাইরে যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সেখানেও জমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
উপজেলা পরিষদের আওতাধীন এলাকায় যে গ্রাম ও গ্রোথ সেন্টারগুলি আছে সেগুলির ভবিষ্যৎ প্রসারের সুবিধার্থে একটি জোনিং ম্যাপ উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে করতে হবে। প্রধান লক্ষ্য থাকবে চাষযোগ্য জমি অকারণে যেন গ্রাম সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত না হয়। গ্রোথ সেন্টারগুলিতে ছোটখাট শিল্প-কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে।
৩.৭ জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের ক্ষেত্রে যদি একাধিক উপজেলা সম্পৃক্ত হয় অর্থাৎ একটি উপজেলার একটি জোন পার্শ্ববর্তী উপজেলাতেও বিস্তৃত হয় তবে সেরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের তত্ত্ববধানে কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।
৩.৮ জাতীয় পর্যায়ে একটি জোনিং ল (Zoning Law) প্রণয়ন করা হবে যার অধীনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের কাজটি করবে। জোনিং ম্যাপ প্রণীত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তার পরিবর্তন করা যাবে না। একান্তই পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তার জন্য কঠিন শর্তাবলী পালনের বিধান Zoning Law-তে অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে। ম্যাপ প্রণয়নের জন্য জেলা প্রশাসকের রাজস্ব অফিসের সহায়তা প্রয়োজন অনুসারে করা হবে।
৩.৯ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকতা/কর্মচারীদের জোনিং ধারণা এবং জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের দক্ষতা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এদেশের এক বা একধিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে।
৪. ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ:
প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভূমির সর্বাধিক ব্যবহার হয়ে থাকে:
ক. কৃষি
খ. আবাসন
গ. বনাঞ্চল
ঘ. নদী, সেচ ও নিষ্কাশন নালা, পুকুর, জলমহাল
ঙ. রাস্তাঘাট
চ. রেলপথ
ছ. বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান
জ. চা ও রাবার বাগান, হর্টিকালচার বাগান
ঝ. উপকূলীয় অঞ্চল
এঞ, চরাঞ্চল
ট. অন্যান্য
৫. কৃষি উৎপাদন:
৫.১ বিগত বছরগুলিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও প্রায় প্রতি বছরই ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়। প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় ২৫ লক্ষ করে এবং বাড়তি প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪.৫ লক্ষ টন। চাষযোগ্য জমির অপরিকল্পিত বা যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে।
৫.২ এদেশে কৃষিভূমি শুধু কৃষিখাতে বা খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নয়। পরিকল্পনা কমিশনের এক হিসাব অনুযায়ী পল্লীঅঞ্চলে বিগত ৮০-র দশকে যে ভূমির প্রায় ১৫ ভাগ কৃষক/গ্রামবাসীদের বসতবাটি ও অকৃষিকাজে ব্যবহৃত হতো বর্তমানে তা প্রায় ৩০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া নগরায়ণ, শিল্পায়ন, আবাসন, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি খাতেও অনেক জমি ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষিজমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এসব অকৃষিখাতে বহুতল ইমারত বানালে ভূমি ব্যবহারে কৃষ্ণতা সম্ভব হবে।
৫.৩ উন্নয়নমূলক অথবা অন্য কোন কাজে ভূমি অধিগ্রহণের সময় অবশ্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা বহু কেইসেই অবলম্বন করা হয় নাই। ফলে বিপুল পরিমাণ উর্বর জমি কৃষিকাজের অযোগ্য ও আওতা-বর্হিভূত হয়ে গেছে। অধিগৃহীত ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ও অপব্যবহার দুই-ই চলছে। বিভিন্ন সময়ে অধিগৃহীত বিপুল পরিমাণ কৃষি ভূমির প্রায় ২৫ ভাগ বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় আছে কিংবা অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভূমির এ ধরনের অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।
৫.৪ কৃষিভূমি সাধারণভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি হলেও এর ব্যবহার সার্বিক জাতীয় ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। এর একটি বিরাট অংশ বর্গাচাষী। এসব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভূমির ব্যবহার এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে এরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কৃষিজমির সার্বিক পরিমাণ বিভিন্ন কারণে উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার বর্তমান ধারা প্রতিহত করতে হবে।
৫.৫ জাতীয় কৃষিনীতিতে ফসল উৎপাদনের জন্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতার নিরিখে সেচযোগ্য জমির আয়তন নির্ধারণ করা জরুরী। এতে একদিকে যেমন মরুকরণ-প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও প্রতিহত হবে অন্যদিকে পানির মত একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। সেচযোগ্য কৃষিজমির অধিগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। উর্বর কৃষিজমি যেখানে বর্তমানে দুই বা ততোধিক ফসল ফলে বা এমন জমি যা এরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময়, তা কোনক্রমেই অকৃষিকাজের জন্য যেমন ব্যক্তিমালিকানাধীন নির্মাণ, গৃহায়ণ, ইটের ভাটা তৈরী ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অকৃষিখাতে উন্নয়নমূলক কাজে ভূমির প্রয়োজন হলে এবং তার জন্য অকৃষি খাস জমি পাওয়া গেলে খাস জমি ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হবে। একেবারেই বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে ন্যূনতম পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি হুকুম দখল করা যেতে পারে।
৬. আবাসন:
গত কয়েক দশকে শহরাঞ্চলের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং পল্লীঅঞ্চল থেকে জনগণের শহরমুখী প্রবাহ ভুমি ব্যবহারের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ বাসস্থান নির্মাণের কাজে ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকা বাদ দিলে দেশের প্রায় সবটাই সমতলভূমি। বাসস্থান নির্মাণের আবশ্যকতায় স্বাভাবিকভাবেই কৃষিজমি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতে শহরাঞ্চলের গৃহায়ণ সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন কঠোরতার সাথে প্রতিপালন ছাড়াও গ্রামীণ জনপদগুলিতে বাসস্থানের জন্য অতিরিক্ত জমি ব্যবহার যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে তার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ ও থানা সদরগুলোতে গৃহায়ণ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শহরাঞ্চলের আবাসিক এলাকাতে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ পরিহার করে নগরবাসীদের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। গ্রামাঞ্চলেও যাতে উর্বর জমিতে গৃহনির্মাণ সংকুচিত করা যায় তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।
৭. বনাঞ্চল:
প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনভূমির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। দেশের মোট বনভূমির অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চল, মধুপুর অঞ্চল, সুন্দরবন ইত্যাদি কিছু এলাকায় বিস্তৃত। জনজীবনের সুস্থতা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞগণ স্থলভূমির অন্তত ২৫% বনাচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সীমিত বনভূমি দেখা যায় তা এই মানদণ্ডে বহু নীচে। তদুপরি দ্রুত নগরায়ণ, ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা স্থাপন, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল ইত্যাদির কারণে যে বায়ু দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। বনায়নের উপযোগী ভূমি ও চরভূমিতে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে এই দূষণ-প্রক্রিয়াকে বহুলাংশে প্রতিহত করা সম্ভব। রিজার্ভ ফরেস্ট ও অন্যান্য বনাঞ্চলে ব্যাপক বন সৃষ্টি এবং বর্তমান বনভূমির সঠিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পরিবেশনীতি, ১৯৯২ ও জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হলে সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।
৮. শিল্পায়ন:
৮.১ বর্তমান বিশ্বের মুক্ত অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে ব্যাপক শিল্পায়নের প্রচেষ্টা নিতে
হবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর উৎপাদন ও বিপণন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি অপরিহার্য। বিগত দশকগুলিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় শিল্প স্থাপনের জন্য বিরাট এলাকা চিহ্নিত করা হয়। ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সংস্থা (বিসিক) কর্তৃক দেশের সর্বত্র এমনকি কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিসিক এস্টেট গঠনের জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের আনুকূল্যে স্থাপিত এই সব শিল্প এলাকায় (শিল্প নগরীতে) বিভিন্ন কারণে প্রত্যাশিত শিল্প স্থাপন ও উৎপাদন কার্যকর হয় নি। বহু এলাকা ভিন্নতর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে বিসিক এলাকাগুলোতে দেখা যায় অধিগৃহীত জমির প্রায় সবটাই, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অন্যদিকে শিল্পনগরীতে খালি প্লট থাকা সত্ত্বেও শিল্পউদ্যোক্তারা হয় প্রয়োজনীয় জমি পাচ্ছে না অথবা সেখানে শিল্প স্থাপনে তারা যে কারণেই হোক উৎসাহী নন। অনেকে শিল্পনগরীর বাইরে কিন্তু অল্প দূরত্বে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন করে উৎপাদন করছেন।
৮.২ বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিতব্য কলকারখানার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কয়েকটি উপাদান গুরুত্ব পেয়ে থাকে তার মধ্যে সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর রেয়াতের সুবিধা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন ও পর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি অন্যতম। সাধারণভাবে দেখা যায় যে প্রধান সড়কগুলোর পাশেই মূলত শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে বলে মনে হয়। দেশের প্রধান সড়কগুলোর দু'পাশে আনুমানিক ৫০০ গজ জায়গা ভবিষ্যত শিল্পায়নের জন্য নির্দিষ্ট রাখা; বিসিক এস্টেটগুলোতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের মালিকরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী না হলে বা অপারগ হলে ঐ প্লটগুলো পুনঃগ্রহণ করে আগ্রহী শিল্পোদ্যোক্তাদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিল্প উৎপাদনে যাওয়ার শর্তে বরাদ্দ প্রদান; বিসিক শিল্পনগরীতে স্থান সংকুলান হলে এর ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোন ক্ষুদ্র/কুটিরশিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সচেষ্ট হতে পারে।
৯. জলাভূমি:
৯.১ এদেশে প্রায় ২৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথ আছে। এই সব নদ-নদী এবং অন্যান্য জলাভূমি মিলে প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বার্ষিক প্রায় ১৪ লাখ টন মৎস্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু সম্ভাবনাময় মৎস্যসম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। বর্তমানে ব্যবহৃত উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়গুলোতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথাযথ মৎস্যচাষ করা হলে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মৎস্য উৎপাদন ২০ লক্ষ টনে উন্নীত করার লক্ষমাত্রা অর্জন সম্ভব হতে পারে।
৯.২ নদীগুলোতে ক্রমাগত পলিমাটি পড়া, যেখানে সেখানে মাটি ভরাট, নিচু এলাকায় পানির স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত করে রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি কারণে জলাভূমি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। এর ফলে নিম্নলিখিত সমস্যার উদ্ভব ঘটে:
ক. বর্ষাকালে বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি;
খ. শুষ্ক মৌসুমে নৌচলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানির অভাব;
গ. সীমিত মৎস্যচাষ;
ঘ. সেচের জন্য অপর্যাপ্ত পানি;
৩. লবণাক্ততা বৃদ্ধি;
চ. জলাবদ্ধতা সমস্যার সৃষ্টি;
ছ. কাপড় কাচা, গোছল করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য পানির স্বল্পতা।
৯.৩ মৎস্য উৎপাদনের জন্য চিরাচরিত ক্ষেত্র, যথা: নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় ইত্যাদি কোনভাবেই যাতে প্রতিকূলতার সম্মুখীন না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর অনেক জায়গাই গ্রীষ্মকালে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এলাকাগুলোতে ব্যাপকহারে কৃষিজমিতে রূপান্তর করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শুধুমাত্র কৃষিজমির আয়তন বাড়ালেই সমস্যার সমাধান ঘটবে না, বরং তাতে নানাবিধ সমস্যা যেমন-প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া, জনগণ কর্তৃক মাছজাত প্রোটিন ঘাটতি ইত্যাদির সৃষ্টি হবে। জাতীয় কৃষিনীতি ও জাতীয় মৎস্যনীতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে যুগপৎ ফসল ও মৎস্যসম্পদ উৎপাদনের প্রচেষ্টা নিতে হবে। বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত চা বাগানগুলো আমাদের রপ্তানী আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য কিছু এলাকায় রাবার বাগান আছে। এছাড়া আছে ফলের বাগান। এসব বিশেষ ধরনের বাগানের সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হবে। এর জন্য বর্তমানে যে জমি ব্যবহৃত হচ্ছে বা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত আছে তা এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত জাতীয় নীতির বহির্ভূত কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এসব জমিতে বিদ্যমান মূল্যবান গাছ নির্বিচারে সংহার করা যাবে না এবং জমির স্বাভাবিক উর্বরতাও বিনষ্ট করা চলবে না।
১০. উপকূলীয় অঞ্চল:
দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রগর্ভ থেকে বিপুল আয়তনের চর জেগে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরো জাগবে। মেয়াদী ভূমি উদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমুদ্রগর্ভ থেকে চর জাগার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে। সমুদ্রগর্ভ থেকে কৃত্রিম উপায়ে চর সৃষ্টির টেকনোলজি ব্যয়বহুল হলেও জাতীয় প্রয়োজনে এই পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন চরভূমিতে বনায়ন, ভূমিহীনদের জন্য আবাসন সৃষ্টি, সর্বসাধারণদের ব্যবহার্য জায়গা/সুবিধার (Public easement) জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিতকরণ, পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ উন্নত চাষাবাদ, ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে হবে। এর জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন আবশ্যক। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে এই কাজটি করা সম্ভব।
১১. চরাঞ্চল:
দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নদীর উভয় পাশে এবং প্রাকৃতিক জলাভূমি যেমন হাওড়-বাওড়, মরা নদী ইত্যাদিতে বহু চর জেগে ওঠে। একটি নীতিমালার মাধ্যমে এই চর ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়া ছাড়াও তাদের জন্য আদর্শগ্রাম ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসন নির্মাণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়ে থাকে। নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে এসব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৩. ভূমির অন্যান্য ব্যবহার:
১৩.১ উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও আরো বহুবিধ কারণে ভূমির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা যথা: শিক্ষা
প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, হাট-বাজার, অফিস-আদালত, নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের কার্য ও আবাসস্থল, ডেইরী ও পোল্ট্রি ফার্ম ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক এ ধরনের স্থাপনা নির্মাণের জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যমান স্থাপনার অতিরিক্ত স্থাপনার ক্ষেত্রে অনায়াসে একটা সীমারেখা টানা যেতে পারে। বিদ্যমান স্থাপনার আয়ত্তাধীন সম্পূর্ণ জমির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে। তারপরেও যদি বাড়তি জমির প্রয়োজন হয় তবে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা নিতে হবে। নদীর নাব্যতা রক্ষণ এবং সেচকাজের সুবিধার্থে নদী খনন করা হয়। এর ফলে যে মাটি পাওয়া যায় তা পরিকল্পিতভাবে ভূমিউন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করতে হবে।
১৩.২ নির্মাণ কাজে ব্যাপকভাবে ইটের ব্যবহার এবং যত্রতত্র ইটের ভাটা তৈরীর ফলে ভূমির শ্রেণীর পরিবর্তনসহ দেশের প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবনতি ঘটেছে। এ অবস্থা রোধকল্পে নির্মাণ কাজে ইটের বিকল্প হিসাবে পাথরকুচি, বালু ও সিমেন্টের তৈরী "হলো ব্লক"-এর ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে যা ভূমিকম্পে দালান-কোঠা ধ্বংসরোধেও সহায়ক হবে।
১৪. অধিগৃহীত জমির অপব্যবহার:
১৪.১ ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ইতিপূর্বে অধিগৃহীত জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ বর্তমানে অব্যবহৃত অথবা অবৈধ দখলের অথবা অপব্যবহৃত অবস্থায় আছে। প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতায় এসব জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। উদ্ধারকৃত জমি সরকার খাসজমি হিসাবে সহজেই পুনঃগ্রহণ (resume) করতে পারে। খাসজমির তালিকায় পুনঃগৃহীত জমির উল্লেখসহ অন্যান্য পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করে তা নিয়মিতভাবে সংশোধন করতে হবে।
১৪.২ ভূমি অধিগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প অধিগৃহীত জমির বহুমুখি ব্যবহার (multilateral use) করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন আনা যেতে পারে। প্রকল্পের স্বার্থে প্রয়োজন কিন্তু বাস্তবে অব্যবহৃত এ ধরনের জমিতে বিশেষ করে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও মহাসড়কের জমিতে দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচী সহায়ক কার্যক্রম যথা: শস্যচাষ, যথোপযুক্ত বৃক্ষরোপণ, পশুপালন, হাঁস-মুরগীর চাষ করা যেতে পারে।
১৫. ভূমি ডেটা ব্যাংক:
১৫.১ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যে সব জমি আছে সেগুলোর বর্তমান ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটা তথ্যভিত্তিক ভূমি ডেটা ব্যাংক চালু করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে এটা প্রণীত হবে। নিম্নলিখিত সূত্রসমূহ থেকে সংগৃহীত ভূমি ডেটা সংরক্ষণ করা হবে:
ক. অব্যহৃত সরকারি খাস জমি;
খ. পতিত জমি;
গ. অধিগৃহীত জমি যা অব্যবহার বা অব্যবহারের জন্য সরকার কর্তৃক পুনঃগৃহীত (resume);
ঘ. ভবিষ্যতে কোন বিশেষ কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট এমন অধিগৃহীত জমি;
ঙ. পয়স্থি চর (নদী থেকে জেগে ওঠা চর) এবং
চ. সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা জমি।
১৫.২ সরকারি খাসজমির (কৃষি ও অকৃষি) ব্যবহার ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত কৃষি ও অকৃষি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালায় বিধৃত নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষিযোগ্য খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কিন্তু অকৃষি খাসজমির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য এর সংরক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। মূলত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এর ব্যবহার সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়।
১৫.৩ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এস্টেট এবং ঢাকা ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর মালিকানায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে কয়েক হাজার একর মূল্যবান সম্পত্তি আছে। কালক্রমে এসব সম্পত্তি অবৈধ দখলদারের হাতে চলে গেছে। এগুলিকে পুনরুদ্ধার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
১৫.৪ সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিমিত্তে প্রায়শঃই স্থাপনা নির্মাণ প্রয়োজন হয়। প্রচলিত বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করা হয়। ভূমির স্থানীয় প্রাপ্যতার আলোকে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। প্রস্তাবিত ভূমি ডেটা ব্যাংক চালু হলে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রথমেই খাসজমির প্রাপ্যতা পরীক্ষা করা হবে। উপযুক্ত খাসজমি পাওয়া গেলে সেটাই বন্দোবস্ত দেয়া শ্রেয় হবে।
১৫.৫ ভূমি ডেটা ব্যাংক তালিকাভুক্ত খাসজমি যদি একান্তই ব্যবহারের উপযুক্ত বিবেচিত না হয় তাহলে জেলা প্রশাসক ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের জন্য সচেষ্ট হবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অধিগৃহীতব্য জমি কোনক্রমেই সেচযোগ্য বা উর্বর কৃষিজমি না হয় এবং জমির পরিমাণও ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে।
১৬. Certificate of Land Ownership (CLO)
ভূমি প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থায় জমির মালিকানাস্বত্ব কোন একটি ডকুমেন্টের ওপর নির্ভরশীল নয়। রেজিস্ট্রিকৃত দলিল, জমির পর্চা এবং সার্ভে ও জরিপ রেকর্ডে নামভুক্তি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ। এতে একদিকে যেমন জমি-সংক্রান্ত বিরোধ ও মামলা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে ভুয়া দলিলের মাধ্যমে নামজারিসহ বিভিন্ন হটকারিতার শিকার হয় নিরীহ জনগণ। এই অবস্থা নিরসনকল্পে একটি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য একক দলিল প্রদানের মাধ্যমে ভূস্বামীর স্বত্ব নিশ্চিত করার প্রায়াস নেয়া হচ্ছে। Certificate of Land Ownership (CLO) স্কীমটি সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হলে খাসজমির ব্যাপক হারে ব্যক্তি মালিকানায় চলে যাওয়ার বর্তমান প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস করা যাবে বলে আশা করা যায়। ভূমি ডেটা প্রণয়ন ও নিয়মিত আপডেটিং-এর ক্ষেত্রে এই স্কীমটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে।
১৭. ভূমি ব্যবহার নীতির মুখ্য দিকসমূহ:
১৭.১ কৃষিজমি যতটুকু সম্ভব কৃষিকাজে ব্যবহার করতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জমির প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন আনা যাবে না;
১৭.২ অনুপস্থিত কৃষিজমি মালিকদের জমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
১৭.৩ কৃষিজমির ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া একটি যৌক্তিক পরিমাণে সীমিত রাখতে হবে;
১৭.৪ সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহ স্ব-স্ব এলাকায় ভূমির ব্যবহারভিত্তিক জোন চিহ্নিত করবে;
১৭.৫ চিহ্নিত জোনসমূহের ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে।
১৭.৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জোনিং ম্যাপ প্রস্তুতকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের রাজস্ব অফিস প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে;
১৭.৭ জোনিং ম্যাপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র এবং শর্তপালন ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাবে না।
১৭.৮ দেশে একটি জোনিং ল (Zoning Law) থাকবে। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জোনিং ম্যাপ এই আইনের ক্ষমতাবলে সকলের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে;
১৭.৯ গ্রামীণ এলাকার জন্য মডেল হাউস নির্মাণ ও পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা তৈরী উৎসাহিত করতে হবে;
১৭.১০ আবাসনের জন্য ব্যবহৃত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে একতলা ভবনের পরিবর্তে বহুতল ভবন নির্মাণকে উৎসাহিত করতে হবে;
১৭.১১ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত বনাঞ্চল বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত থাকবে;
১৭.১২ বর্তমানে ব্যবহৃত বনভূমির সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
১৭.১৩ উপকূলীয় অঞ্চলে কার্যকরভাবে বনাঞ্চলের সবুজ বেষ্টনী সৃজন করতে হবে;
১৭.১৪ সামাজিক বনায়নকে উৎসাহিত করতে হবে;
১৭.১৫ বিদ্যমান জলাশয় উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং তা ভরাট করা যাবে না। এ দায়িত্ব ব্যক্তি মালিকানাধীন ছোট পুকুরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিকের ওপর এবং বৃহৎ জলাশয় যেমন-নদী, খাল, হাওড়-বাওড় এবং বিল-এর দায়িত্ব ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী ও সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জলাশয়সমূহের নিয়মিত সংস্কার ও পুনঃখনন প্রয়োজন হবে;
১৭.১৬ যতদূর সম্ভব বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধকে সড়ক/রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা হবে;
১৭.১৭ বাঁধে পরিকল্পিত উপায়ে উপযুক্ত বৃক্ষরোপণ করতে হবে;
১৭.১৮ বাঁধ নির্মাণের জন্য খননকৃত খাদ/গহ্বর জলাশয় হিসাবে মৎস্য উৎপাদন ও হাঁস পালনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরী করার সময় যতদূর সম্ভব নতুন জলাশয় সৃষ্টি না করে আশপাশে অবস্থিত ভরাট জলাশয় পুনঃখনন করে বাঁধের জন্য প্রয়োজনীয় মাটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১৭.১৯ বাঁধ নির্মাণের ফলে যাতে করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;
১৭.২০ শুধুমাত্র জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক সড়ক ও জেলা-উপজেলা, উপজেলা-উপজেলা সংযোগকারী সড়ক ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। যে সব ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ একান্তই অপরিহার্য সেখানে বসতবাড়ি ও উর্বর কৃষিজমি যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে অন্তগ্রাম/আন্তগ্রাম রাস্তা নির্মাণ পরিকল্পিত উপায়ে হতে হবে।
১৭.২১ শিল্প স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট জোনে নতুন শিল্প-কারখানা নির্মাণ করতে হবে। এর জন্য শিল্প সহায়ক সেবাসমূহ যাতে সহজলভ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;
১৭.২২ কোন নির্দিষ্ট প্রকৃতির শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য চিহ্নিত অঞ্চলে শুধুমাত্র সেই প্রাকৃতিক কারখানা স্থাপনযোগ্য হবে;
১৭.২৩ শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন/নির্গমনের যথাযথ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে ভূমি বা পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয়;
১৭.২৪ দেশের প্রধান সড়কসমূহে যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রধান সড়কসমূহের দুই পার্শ্বে "সার্ভিস লেইন"-এর ব্যবস্থা রাখা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে প্রধান সড়কসমূহের দুই পার্শ্বে বনায়নের জন্য ১০ হতে ২০ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে;
১৭.২৫ বিসিক শিল্পনগরীতে স্থান সংকুলান হলে এর ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্য কোন ক্ষুদ্র/কুটিরশিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করতে হবে;
১৭.২৬ চা-বাগান, রাবার বাগান ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত জমি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চা-বাগানের জমি কোন অবস্থাতেই চা-চাষ বর্হিভূত কাজে ব্যবহার করা যাবে না;
১৭.২৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহকে জরিপ কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত করা হবে;
১৭.২৮ বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী উপ-সম্প্রদায়গুলোকে প্রচলিত আইন মোতাবেক ভূমির অধিকার প্রদানসহ তাদের সমাজগত অধিকার সংরক্ষণ করা হবে।
১৮. জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ:
কোন জাতীয় নীতিই পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা যায় না যদি না বৃহত্তর গোষ্ঠির কাছে এটা বোধগোম্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। ভূমিনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দেশে কৃষিজমির সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের অপরিহার্যতা, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ব্যাপক মৎস্যচাষের প্রয়োজনীয়তা, বনায়ন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যাবে না। মানুষ যখন এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ হবে তখন গৃহ নির্মাণের জন্য তার উর্বর ভূমিখণ্ড সে সহজে ব্যবহার করবে না। বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে সে নিজে থেকেই সচেষ্ট হবে।
১৯. জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি (National Land Use Committee):
১৯.১ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হবে:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভাপতি
ভূমি মন্ত্রী সহ-সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সদস্য
অর্থ মন্ত্রী সদস্য
শিক্ষা মন্ত্রী সদস্য
পানিসম্পদ মন্ত্রী সদস্য
শিল্প মন্ত্রী সদস্য
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সদস্য
কৃষি মন্ত্রী সদস্য
যোগাযোগ মন্ত্রী সদস্য
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী সদস্য
পরিবেশ ও বন মন্ত্রী সদস্য
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সদস্য
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী সদস্য
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী সদস্য
পরিকল্পনা মন্ত্রী সদস্য
মন্ত্রিপরিষদ সচিব সদস্য
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সদস্য
সংশ্লিষ্ট সচিবগণ সদস্য
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
(এফবিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় সদস্য-সচিব
১৯.২ ভূমি মন্ত্রণালয় জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সেবা/সহায়তা প্রদান করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে এবং সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।
২০. জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত একটি ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে:
ভূমি মন্ত্রী আহবায়ক
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সদস্য
কৃষি মন্ত্রী সদস্য
যোগাযোগ মন্ত্রী সদস্য
পরিবেশ ও বনমন্ত্রী সদস্য
পরিকল্পনা মন্ত্রী সদস্য
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সদস্য
সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সদস্য
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সদস্য
সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সদস্য
সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সদস্য
সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় সদস্য-সচিব
২০.১. ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সেবা/সহায়তা প্রদান করবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে এবং সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।
এম, সাইফুল ইসলাম
সচিব।

মন্তব্যসমূহ (0)
মন্তব্য করতে লগইন করুন।
এখনও কোনো মন্তব্য করা হয়নি। প্রথম মন্তব্যকারী হোন!